৬ষ্ঠ শ্রেণি ৪র্থ সপ্তাহের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় অ্যাসাইনমেন্ট উত্তর ২০২২
৬ষ্ঠ শ্রেণি ৪র্থ সপ্তাহের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় অ্যাসাইনমেন্ট উত্তর ২০২২ | Class 6 Bangladesh o bisso porichoy 4th week assignment 2022
ক নং প্রশ্নের উত্তর
ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে পুরনো সভ্যতা হলো সিন্ধু সভ্যতা।রএ সভ্যতা খ্রিষ্টপূর্ব ২৭০০ অব্দে ভারত উপমহাদেশের সিন্ধু, সরস্বতী, হাকরা ইত্যাদি নদ – নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠে। এ সভ্যতার বড় দুইটি নগরের একটি হরপ্পা আর অন্যটি মহেঞ্জোদারো। সিন্ধু সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতা নামেও পরিচিত। নিচে সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য দেওয়া হলো:
১. সিন্ধু সভ্যতা ভারত উপমহাদেশের প্রথম নগর সভ্যতা।
২. এ সভ্যতার নগরগুলোতে উন্নত নগর পরিকল্পনা ছিল। নগরে রাস্তা , রাস্তার পাশে ডাস্টবিন , সড়ক বাতি , পানি নেমে যাওয়ার জন্য ড্রেন সব কিছুই ছিল একেবারে সাজানো।
৩. এ সভ্যতার একতলা – দোতলা ঘরবাড়িগুলো পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছিল। প্রত্যেক বাড়িতে পানির জন্য ছিল কুয়া , ছোট ড্রেন দিয়ে বাড়ির ময়লা পানি চলে যেত রাস্তার বড় ড্রেনে।
৪. এ সভ্যতায় ছিল অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য ব্যবস্থা।
৫. সিন্ধু নগরীর হরপ্পাতে পাওয়া গেছে শস্য জমা রাখার জন্য বিশাল শস্যাগার।
৬. পোড়ামাটির বেশ কয়েকটি মূর্তিও পাওয়া গেছে সিন্ধু সভ্যতায়। পাওয়া গেছে চুনা পাথর ও ব্রোঞ্জের মূর্তি।
খ নং প্রশ্নের উত্তর
সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার ভারতীয় তথা বিশ্বের সভ্যতার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মানব সভ্যতার বিকাশ সম্বন্ধে ইহা বহু প্রাচীন ধারণার পরিবর্তন সাধন করেছে। সিন্ধু সভ্যতা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা। নিচে উন্নত নগর পরিকল্পনার সাথে সিন্ধু সভ্যতার সাদৃশ্য দেওয়া হলো –
১. নগর পরিকল্পনা:
খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় নগরগুলি পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি। সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার প্রধান নগর ছিল মহেঞ্জোদারো হরপ্পা। হরপ্পা সভ্যতার নগর গুলির নির্মাণ কৌশল ও স্থাপত্যবিদ্যা , নাগরিক স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সুযোগ – সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে নগর পরিকল্পনা করা হয়েছিল।
২. নগর দুর্গ ও শস্যাগার :
নগরের উঁচু স্থানে নগর দুর্গ ছিল। এখানে সম্ভবত শাসকশ্রেণীর বাস করত । এই দুর্গের আশেপাশে বড় বড় ইরামত গুলিতে প্রশাসনিক কাজকর্ম হত। নগর দুর্গের নিচে ছিল সাধারণ নগরাঞ্চল।
৩. শস্যাগার :
হরপ্পার শস্যাগার টি নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে নদী পথে এসে শস্যগারে জমা হতো। এই শস্যগারগুলি শস্য ব্যাংক হিসাবে ব্যবহার হতো। ইতিপূর্বে এক ধরনের শস্যাগার পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায়নি। বন্যা হলে এই শস্যাগার থেকে শস্য নাগরিকদের দেওয়া হতো।
৪. স্নানাগার :
মহেঞ্জোদারোর নগর দুর্গের বাইরে এক বিশাল স্নানাগার পাওয়া গিয়েছে। এই স্নানাগারে আয়তন ১৮০ ফুট ও প্রস্থে ১৮ ফুট এর চারিদিকে ৪ ফুট উঁচু পাঁচিল ছিল। স্নানাগারের কেন্দ্রস্থলে ছিল একটি জলাশয়। এই জলাশয় টি ৩৯ ফুট লম্বা ২৩ ফুট চওড়া ও ৪ ফুট গভীর ছিল।
৫. বাড়িঘর , রাস্তাঘাট , জল নিকাশি ব্যবস্থা :
নগরের পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং উত্তর – দক্ষিণে সমান্তরাল কয়েকটি পাকা রাস্তা ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর রাস্তাগুলি ৯ ফুট থেকে ৩৪ ফুট পর্যন্ত চওড়া ছিল। রাস্তাগুলো পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিকে পরস্পরকে সমকোণে খন্ডিত করে নগরকে কয়েকটি আয়তক্ষেত্রে পরিণত করেছিল।প্রধান রাস্তার পাশে গলিপথে গৃহের প্রবেশদ্বার ছিল। ছোট – বড় সব বাড়িতে কুয়ো ও স্নানাগার ছিল।
বাড়ি থেকে ময়লা জল নিষ্কাশিত হয় বড় রাস্তার নর্দমায় পড়তো। বড় রাস্তার ধারে ঢাকা নর্দমা ছিল। নর্দমার আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য ম্যানহোল থাকতো। রাস্তার ধারে ডাস্টবিন ছিল। সারিবদ্ধ ছোট ছোট কুঠুরি ঘরে শ্রমিক ও দরিদ্র মানুষেরা বাস করত। শহরের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি শাসকদের দৃষ্টি ছিল।
গ নং প্রশ্নের উত্তর
উয়ারী – বটেশ্বর :
উয়ারী – বটেশ্বর নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার দুইটি গ্রামের বর্তমান নাম। প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত উয়ারী – বটেশ্বর গ্রামে আড়াই হাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল নগর সভ্যতা। উয়ারী বটেশ্বর ছিল সেই নগর সভ্যতার নগর কেন্দ্র। আড়াই হাজার বছর পূর্বে গড়ে উঠা নগর সভ্যতা একদিন ধ্বংস হয় ; মাটির নিচে চাপা পড়ে। পরবর্তীতে উয়ারী – বটেশ্বর অঞ্চলে জমি চাষ , গর্ত খনন প্রভৃতি
গৃহস্থালি কাজে ভূমির মাটি ওলট – পালট হয়।
প্রাচীন নিদর্শন ভূমির উপর চলে আসে। বর্ষাকালে বৃষ্টির পর ধাতব , কাচ ও পাথরের প্রত্নবস্তুগুলোও চকচকে উয়ারী – বটেশ্বরে প্রাপ্ত ধাতব অলংকার , স্বল্প মূল্যবান পাথর ও কাচের পুঁতি , চুন – সুরকির রাস্তা , ইট নির্মিত স্থাপত্য , দুর্গ প্রভৃতি একটি সমৃদ্ধ সভ্যতার পরিচয় বহন করে।
ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা এবং নয়নাভিরাম বাটখারা বাণিজ্যের পরিচায়ক। উয়ারী – বটেশ্বর ছিল একটি নদীবন্দর। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল উয়ারী – বটেশ্বর। রোলেটেড মৃৎপাত্র ও স্যান্ডউইচ কাচের পুঁতির আবিষ্কার উয়ারী – বটেশ্বরকে ভূমধ্যসাগর এলাকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করে। নবযুক্ত হাইটিন ব্রোঞ্জ নির্মিত পাত্র দক্ষিণ – পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে উয়ারী – বটেশ্বরের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা বলে।
মহাস্থানগড় পুণ্ড্রনগর :
প্রায় ২৪০০ বছর আগে বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৮ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে গড়ে উঠে মহাস্থানগড় ( পুণ্ড্রনগর )। নগরটি ছিল ধন – সম্পদে পরিপূর্ণ। তাই দুর্গপ্রাচীর ও পরিখা দ্বারা সেটি ছিল সুরক্ষিত। কালের পরিক্রমায় পুণ্ড্রনগর ধ্বংস হয়ে মাটির নিচে চাপা পড়ে ঢিপি ও জঙ্গলে পরিণত হয়।
দেশপ্রেমিক ফকির মজনু শাহ মহাস্থানগড় জঙ্গল থেকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করতেন। মানুষ ভুলে যায় প্রাচীন নগরের আসল নাম। প্রত্নতাত্ত্বিক আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৭৯ সালে মহাস্থানগড়ে জরিপ করে অনুমান করেন এখানকার মাটির নিচে লুকিয়ে আছে বিখ্যাত পুণ্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ। শুরু হয় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ। আবিষ্কার হতে থাকে নগরের রাস্তাঘাট , ঘরবাড়ি , অলংকার , মুদ্রা , পোড়ামাটির শিল্পকর্ম , লিপি প্রভৃতি।
৫-১০ মি . উঁচু দুর্গপ্রাচীর পরিবেষ্টিত খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের নগরকেন্দ্রটি ছিল উত্তর – দক্ষিণে ১৫২৩ মি . এবং পূর্ব পশ্চিমে ১৩৭১ মি .। অনুমিত হয় জনহিতৈষী মৌর্য শাসক সম্রাট অশোক পুণ্ড্রনগর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। ব্রাহ্মী লিপিতে পুণ্ড্রনগরে দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদের শস্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করার আদেশ লিপিবদ্ধ আছে। এও বলা হয়েছে যে , সুদিন ফিরে আসলে প্রজাসাধারণ যেন আবার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তা ফেরত দেন।

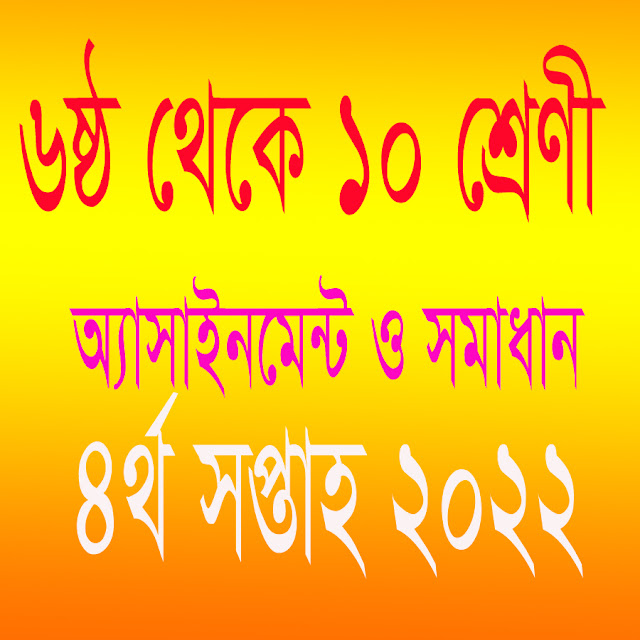



0 Comments